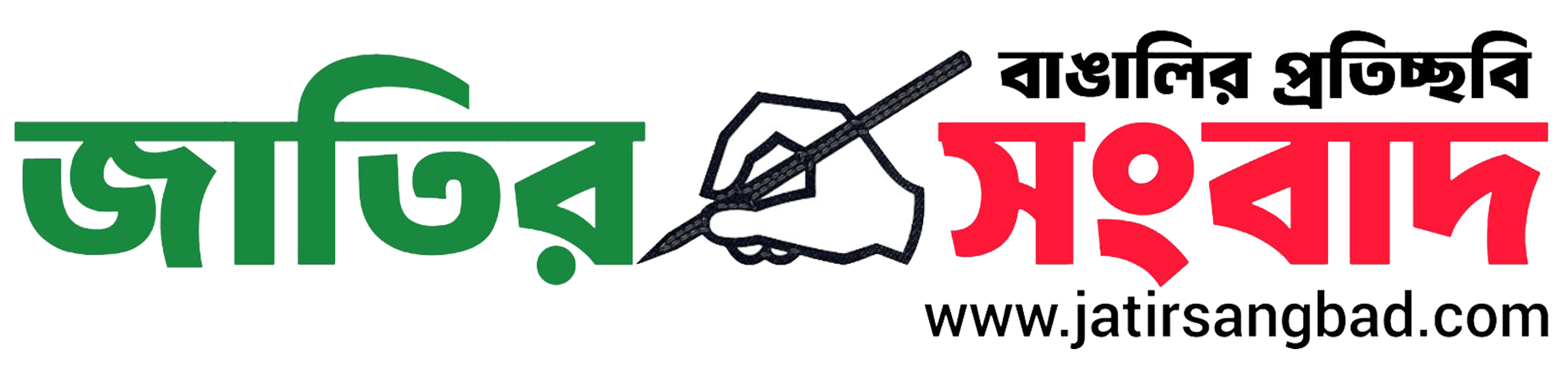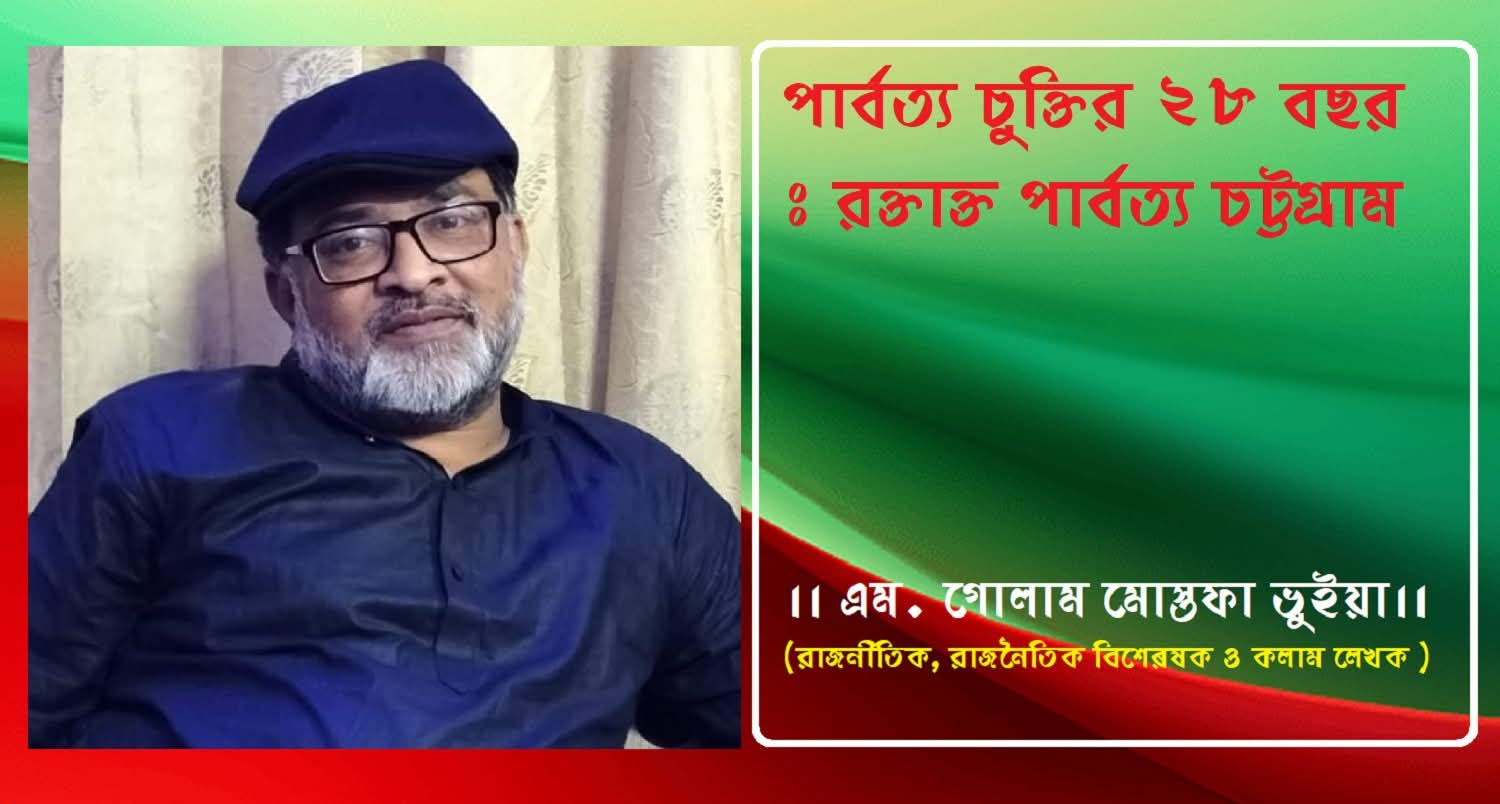
।। এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া।।
১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিকে দেশপ্রেমিক জনগোষ্টি কালো চুক্তি হিসাবেই অবিহিত করে থাকে। এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শুধু মাত্র একটি গোষ্টির স্বার্থ রক্ষা হলেও বাঙ্গালী জনগোষ্টি স্বার্থ ক্ষুন্ন করা হয়েছে। ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ পার্বত্য শান্তি চুক্তি তথা কালো চুক্তির ২৮ বছর পূর্তি। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়ন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনা এখনো চলমান। চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে দুই পক্ষই একে অপরের প্রতি অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে ব্যস্ত। আর সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কতিপয় ধারা সংশোধন করে পার্বত্য চুক্তি পুনঃমূল্যায়নের দাবি তুলে ধরা হচ্ছে গত ২৮ বছর যাবতই।
বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে সন্ত্রাস ও হত্যার ইতিহাস দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক। খাগড়াছড়িতে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনা তারই অংশ। ব্রিটিশ শাসনের সময় এই অঞ্চল সরাসরি ব্রিটিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তখন স্থানীয় পাহাড়ি রাজা ও সম্প্রদায়কে আঞ্চলিক শাসনের অধিকার দেয়া হয় এবং জমির মালিকানা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মূলত উপজাতীয় সমাজের হাতে রাখা হয়, ফলে তাদের সামাজিক কাঠামো ও স্বায়ত্তশাসন মজবুত ছিল। পাকিস্তান আমলেও পার্বত্যাঞ্চল অবহেলার শিকার হয়। সে সময় কেন্দ্রীয় শাসন স্থানীয় অধিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে ‘বিভক্ত করো ও শাসন করো’ নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। এর ফলে জমি দখল, প্রশাসনিক নিপীড়ন ইত্যাদি কারণে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে; তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা অথবা বাইরের রাজনৈতিক প্রভাবে হত্যা, অপহরণ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।
এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই বেশিরভাগ সময় ধরে চলে রক্তক্ষয়ী সংঘাত। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালিন আওয়ামী লীগ সরকার আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে সম্পাদিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এটি শান্তি চুক্তি নামেই বেশি পরিচিত। তৎকালীন সরকারের পক্ষে সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও পাহাড়িদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় ওরফে সন্তু লারমা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির লক্ষ্য পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা থাকলেও আজও সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন হয় নাই। চুক্তির পর কেটে যায় ২৮ বছর। পাহাড়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলেও কাঙ্ক্ষিত শান্তির দেখা পাননি পার্বত্যবাসী। অস্ত্র সমর্পণ করে চুক্তি সম্পাদন করা হলেও পাহাড়ে এখনও অবৈধ অস্ত্র নিয়ে বিচরণ করছে পাহাড়িদের অন্তত ছয়টি গ্রুপ। অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার, অপহরণ, খুন ও চাঁদাবাজির কারণে অস্থির পার্বত্য চট্টগ্রাম। চুক্তির পরও পাহাড়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি থামেনি। ফলে উন্নয়ন কাজে পাহাড়ের প্রতিটি স্তরে চাঁদা দিতে হচ্ছে। এদিকে চুক্তির পর পাহাড়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। বাঙ্গালী জনগোষ্টির মতে, পার্বত্য চুক্তিতে সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে তাদের। শান্তি চুক্তি হচ্ছে পার্বত্য এলাকার জন্য একটি কালো চুক্তি। এ চুক্তির ফলে এক পক্ষ লাভবান ও অন্যপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু ধারা পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে সাংঘর্ষিক বলেও মনে করেন তারা। স্থানীয়দের ধারণা, পাহাড়ে প্রকৃত শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে হবে এবং চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।
১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে পার্বত্য জেলাগুলোতে শান্তিবাহিনী ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষে প্রায় ৪০০ সেনা ও ৩০ হাজার বাঙালি নিহত হয়—শত শত পরিবার বাস্তুচ্যুত ও সম্পদ ধ্বংসের শিকার হয় এবং নিরাপত্তাহীনতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই সময়ে তথাকথিত মানবাধিকারকর্মী, বামপন্থি ও ভারতপন্থি বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা ও কখনো কখনো উসকানিমূলক ভূমিকার অভিযোগও ওঠে; ফলে সংঘাত আরও জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী রূপ নেয়। ১৯৯৬-৯৭ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সংঘাত কমার বদলে নতুন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সংগঠিত ঘটনাবলির পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবে স্থায়ী সমাধান আনতে ব্যর্থ হয়েছে; বরং কিছু ক্ষেত্রে এটি প্রশাসনিক বিভাজন, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, সম্পদ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডকে থামাতে পারেনি এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব বজায় রাখতে সাহায্য করেছে বলে অভিযোজনা রয়েছে। চুক্তির প্রক্রিয়ায় ইউপিডিএফ ও জেএসএসকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এটাকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন।
পার্বত্য চুক্তির ২৮ বছরেও চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির তুলনায় ইসলাম ধর্মের বাঙ্গালী, বড়ুয়া, তনচঙ্গা,সাঁওতাল, অহমিয়া, গুর্খা, কুকি, পাংখোয়া, লুসাই (মিজু), চাক, খুমি, খিয়াং ও ম্রো জনগোষ্ঠীর সদস্যরা ২৮ বছরে অনেক বেশী পিছিয়ে পড়েছে। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক এটাই সত্য। পার্বত্য অঞ্চলের বসবাসরত অধিবাসীদের যে রাজনৈতিক অধিকার ছিল চুক্তির পর ২৮ বছরেও আদৌ তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হবার মুল কারণ হচ্ছে : উগ্র সম্প্রদায়িকতা, বৈষম্য ও সীমাহীন ক্ষমতার লোভ। পার্বত্য অঞ্চলে ৯০% রাষ্ট্রীয় সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে তিনটি জনগোষ্ঠীর লোকজন। বাকি ১০% বাঙ্গালী, বড়ুয়া, তনচঙ্গা, সাঁওতাল, অহমিয়া, গুর্খা, কুকি, পাংখোয়া, লুসাই (মিজু), চাক, খুমি, খিয়াং ও ম্রো জনগোষ্ঠীর লোকজন, বিশাল ধরনের বৈষম্যে এ অঞ্চলে চলমান। যার কারণে সহজ-সরল জনগোষ্ঠীর লোকজন ছোট-ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছে। আগামীতে আরো কয়েকটি জনগোষ্ঠীর লোকজন অস্ত্র হাতে তুলে নিবেনা তার কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে বলে মনে হয় না।
১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে এই অঞ্চলের রাজনীতি অনেকটাই বদলে গেছে। পার্বত্য চুক্তির এক বছরের মধ্যেই চুক্তির পক্ষের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস-মুল) সঙ্গে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ-মুল), রক্তক্ষয়ী সংঘাত শুরু হয়, যা একনো চলমান। ২০০৭ সালে পিসিজেএসএস-মুল ভেঙে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস-সংস্কারপন্থি বা এমএন লারমা) নামের নতুন রাজনৈতিক দল। ২০১৭ সালে খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয়। ওই বছরের ১৫ নভেম্বর তপন জ্যোতি চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক নামের নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই চারটি উপ দল বা গ্রুপের বাইরেও আরও কয়েকটি গ্রুপ বা উপদল সক্রিয় রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) অন্যতম। এই দলের সদস্যদের অবস্থান বান্দরবানের গহিনে। ২০১৮ সালে এএলপি ভেঙে গঠিত হয় মগ পার্টি ও কুকি চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট ইত্যাদির জন্ম হয়। তাদের অবস্থানও বান্দরবানে। তবে এই তিন দলের অবস্থান শুধু বান্দরবানে, রাঙামাটি কিংবা খাগড়াছড়িতে এদের কোনো তৎপরতা নেই। বাংলাদেশ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করলেও সংগঠনটির পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, দাবি তারা বাংলাদেশের কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন নয়। একইসঙ্গে তারা জানিয়েছেন, তাদের ভাষায়, “সুবিধা বঞ্চিত কুকি-চিন জনগোষ্ঠীর জন্যে স্বশাসিত বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাসহ একটি ছোট রাজ্য” চাইলেও তারা কোন স্বাধীনতার ঘোষণা করে নাই। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানা যায়, কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট এর অস্ত্রধারী সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মির ভারতের মিজুরাম প্রদেশে ৩ হাজার অস্ত্রদারী সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মির সদস্যদের র্যাব বাহিনী গ্রেফতার করে রাঙামাটি কারাগারে আটক করে রাখছেন। কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা জামিনে ছাড়া পাওয়ার তথ্য নাই। এদের নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করতে একটি মহলের ষড়যন্ত্র চলছে বলে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের ধারনা।
তিন পার্বত্য জেলায় প্রায় ১৪ লাখ মানুষের মধ্যে আনুমানিক ৫৯ শতাংশ বাঙালি ও ৪১ শতাংশ পাহাড়ি বলে মনে করা হয়। তবে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বাঙালি ও পাহাড়ি উভয়ের উপস্থিতি গঠনগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের হত্যার বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা আরো সাহসী হয়ে ওঠে এবং কিছু ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রীয় আশ্রয়ও পেয়েছে, যা দেশের জন্য লজ্জাজনক। একই সাথে শিক্ষাগত দিক থেকেও কিছু পার্থক্য রয়েছে; বলা হয়, চাকমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে বেশি এবং চাকমা নারীদের মধ্যে শিক্ষকতা পেশায় অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, কয়েকটি এলাকার বাঙালি জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত হার কমে আসছে। এসব পার্থক্য প্রশাসনিক নীতিতে এবং উন্নয়ন উদ্যোগের বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলে যেখানে কখনো বাঙালির দুরবস্থা উপেক্ষিত থেকে যায়। পাশাপাশি কিছু পাহাড়ি এলাকায় জমি লিজ দেয়া ও পরিচালনার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, যা রাষ্ট্রীয় ন্যায়বিচার ও নাগরিক অধিকারের দিক থেকে বিতর্কিত।
একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তখনই অর্থবহ হয় যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। স্বাধীনতার পর দেশের অগ্রগতির পথে বাধা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল। পার্বত্য চুক্তির পর পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত স্ব-স্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা থাকলেও ২৮ বছরে সামাজিক অধিকারের বিষয়ে বলতে গেলে বরঞ্চ সংঘাত, গুম, খুন হানাহানি আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার পার্বত্য অঞ্চলের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে একজন নাগরিকের জন্মগত মৌলিক অধিকার ৫টির মধ্যে অন্যতম শিক্ষার অধিকার স্থানীয়দের হাতে ন্যস্ত করে পার্বত্যঞ্চলের বসবাসরত অধিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে ২৮ বছরে শিক্ষার মেরুদন্ডই ভেঙ্গে পড়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় গিয়ে দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষকদের উপস্থিতি নেই। একটি বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক মিলে একজন বর্গা শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে রেখেছেন, আর জেলা পরিষদ সমূহ ঘুষ বাণিজ্যের মাধ্যমে যাদের শিক্ষক পদে নিয়োগ দিয়ে থাকে তারা কখনো নিজেদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকেন না। তা ছাড়া বেশী ভাগ শিক্ষক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছেলে,মেয়ে,আত্ময়ী-স্বজন। পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা খাতে যে বরাদ্ধ রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে ব্যয় করা হয় তা কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এসবের সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা পায়না।
বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হচ্ছে, আরাকান আর্মি পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু উপজাতি যুবককে প্রশিক্ষণ দেয়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে আর একই সাথে তারা অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় অবাধে বিচরণ করছে। আরাকান আর্মির সদস্যদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে। বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় ছয় হাজার যুবক সক্রিয়ভাবে কাজ করছে যারা আরাকান আর্মির কাছ থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে। আরাকান আর্মি চাইলে তাদের দিয়ে সর্বাত্মক গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে পারে। বান্দরবানের গহিন জঙ্গলের অনেক স্থানেই রয়েছে আরাকান আর্মির সদস্যরা। রাঙ্গামাটি এমনকি খাগড়াছড়িতেও তাদের অবস্থানের সংবাদ পাওয়া যায়। এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য সত্যিকার অর্থেই ভীতিকর। বিশেষত তাদের সাথে একটি বৃহৎ শক্তির সংবেদনশীল সম্পর্ক থাকায় বাংলাদেশের জন্য নিরাপত্তা উদ্বেগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে সন্তু লারমা দলের ৭৩৯ জন অকেজো কিছু অস্ত্রসহ কথিত আত্মসমর্পণ করে। প্রায় ৬৪ হাজার জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। অবশ্য এই পার্বত্য চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ পুরুস্কার পেয়েছে। যেমন,‘ওয়াশিংটন পোস্ট’ পত্রিকা মন্তব্য করে, ‘এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের একটি বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে।’ ইউনেস্কো বাংলাদেশের এই পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন করায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে। কিন্তু চুক্তির মৌলিক প্রধান শর্ত ছিল, অবৈধ অস্ত্র পরিহার পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। দুঃখজনক যে, চুক্তির ২৮ বছর পেরিয়ে গেলেও সন্তু লারমার জেএসএস সম্পূর্ণ অবৈধ অস্ত্র সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি।
পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর অনেক জায়গায় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো স্থানীয় রাজনীতি ও প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করে; চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক দখলদারির ঘটনা নিত্যসংবাদে পরিণত হয়। একদিকে প্রশাসনিক উপস্থিতি দুর্বল হয়ে পড়ায় জনগণের নিরাপত্তা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অন্যদিকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ বা বাইরের প্রভাব চুক্তিকে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধিতে লিপ্ত রয়েছে—এগুলো সব মিলিয়ে জনমানসে আস্থা হ্রাস করেছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বাস্তব উন্নয়ন কাজেও বাধা এসেছে; যদিও সরকারি নীতিতে প্রায়ই ‘পাহাড়িদের উন্নয়ন’কে গুরুত্ব দেওয়া হয়, স্থানীয় বাঙালিদের দুরবস্থার বিষয়টি নানাবিধ কারণে উপেক্ষিত থেকে যায়।
বর্তমানে খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীলতা হ্রাস ও নিয়ন্ত্রন করতে সেনা ক্যাম্প ও ক্যান্টনমেন্ট বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠেছে; বিশেষত কিছু সম্ভাব্য সুপারিশে খাগড়াছড়িতে ক্যাম্প সংখ্যা ২৫০-তে উন্নীত করার কথা বলা হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তির পরে সেনা ক্যাম্প কমানো হয়েছিল, যা নিরাপত্তাহীনতার প্রশস্তির ভাব প্রকাশ করেছে বলে মনে করা হয়; যদিও অধিকাংশ মানুষ মনে করেন সেনা উপস্থিতি বাড়লেই নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, অন্যরা আশঙ্কা করেন এতে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই সেনা ক্যাম্প এবং সেনা উপস্থিতি বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় স্থানীয় মতামত, নিরাপত্তা পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও মানবাধিকার বিবেচনা করে আসন্ন নীতি গ্রহণ করা উচিত।
পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার মূলে আছে বহুমুখী ও জটিল ভূ-রাজনৈতিক অনুষঙ্গ। এই সঙ্কটকে কেবল জাতিগত বা ধর্মীয় দ্বন্দ হিসেবে দেখলে তাতে বাস্তব সমাধান মিলবে না; এটি মূলত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অংশগ্রহণমূলক নীতি-নির্ধারণের প্রশ্ন। বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্যাঞ্চলকে ভিন্ন আইনি পরিচয়ে ভাগ করা হয়নি, সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। তাই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত পুরো দেশের মানুষের সার্বিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। মনে রাখতে হবে, তথা কথিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির সাথে যেহেতু বাংলাদেশ সংবিধানের সাংঘর্ষিক অবস্থান রয়েছে তাই, সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ধারা সংবলিত চুক্তি সংশোধন করা উচিত এবং চুক্তির বৈষম্যেমূলক ধারা-উপধারায় পার্বত্য বাঙালিরা পিছিয়ে পড়েছে। চুক্তিতে বাঙালিদের জন্যও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এবং পাহাড়ের সকল পক্ষের সাথে বৃহত্তর আলোচনা করা প্রয়োজন সরকারের। এছাড়াও প্রত্যাহারকৃত সেনা ক্যাম্পগুলো দ্রুত স্থাপন করা প্রয়োজন।
(লেখক : রাজনীতিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক )
E-mail : gmbhuiyan@gmail.com